লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা হল লোকসাহিত্য। লোকসংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগে যাকে বাককেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলে আপনারা জেনেছেন, আসলে সেটাই হল লোকসাহিত্য।
এই সংজ্ঞায় 'লোক' বলতে যাদের বুঝি তারা আর কেবল গ্রামীণ কৃষিজীবী সম্প্রদায় নন, নন কেবল নিরক্ষর সংহত সমাজের সদস্য – এখানে গ্রাম-শহরের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মৌখিক ও লিখিতের, কৃষি ও শিল্পের সকল ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। নিরক্ষরের পাশাপাশি, শিক্ষিত মানুষও হয়ে যান লোক বা Folk.
সেই লোকসমাজের ‘সৃষ্ট' সাহিত্য লোকসাহিত্য, সৃষ্ট কিন্তু লিখিত নয়, এই কারণে যে, লোকসাহিত্য মুখ্যত মৌখিক। লোকসাহিত্য মৌখিক কথা নির্ভর। তার কোন লিখিত রূপ যেমন (সংরক্ষণ ব্যতীত) দরকার হয় না, তেমনি তার কোন নির্দিষ্ট রচয়িতা বা স্রষ্টা নেই।
শিষ্ট সাহিত্য যেখানে ব্যক্তির সৃষ্টি, লোকসাহিত্য সেখানে সমষ্টির সৃষ্টি। লোকসমাজের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এর সামাজিক সংহতি। লোকসমাজ এমনই সংহত যে, এর যে কোন সৃষ্টিতে স্রষ্টা খুঁজে পাওয়া ভার লোকসংস্কৃতির যে কোন দিকেই একথা সত্য। তাই বলে -
লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির যে কোন রূপ কখনই লোকসমাজের সকল মানুষ একজায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করে সৃষ্ট নয়, তার এক একটা ধারার সৃষ্টির পিছনে কোন না কোন একক মানুষের ভূমিকা শুরুতে হয়তো ছিল, কিন্তু সংহত সমাজের সমবেত আওয়াজের ভীড়ে হারিয়ে গেছে সেই একক মানুষের একক চেষ্টার নজির।
তাই সব মিলিয়ে, লোকসাহিত্য কাকে বলে? এর উত্তরে বলা যায় - লোকসাহিত্য হল সংহত একদল মানুষের সমবেত সাহিত্য সৃষ্টি, যা মূলত মৌখিক ও ঐতিহ্যবাহী, যার সৃষ্টি লিখন নয়, মুখের ভাষাকেন্দ্রিক।
লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তা নিরক্ষর জনগণের সাহিত্য। এ পরিচয়ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ লোকসাহিত্য আর নিরক্ষরের সাহিত্য নয়, তা শিক্ষিত মানুষেরও সাহিত্য। তবে, লোকসাহিত্য তখনই শিক্ষিত মানুষের বা নাগরিক মানুষের লোকসাহিত্য হয়, যখন নাগরিক শিক্ষিত মানুষ 'লোক' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। যখন কোন একটা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সামাজিক বেশ কিছু মানুষ এক হন বা সংহত হন, সে গ্রামের নিরক্ষর কিংবা শহরের শিক্ষিত, কৃষিজীবী কিংবা কারখানার শ্রমিক তখন সে সংহত জনসমষ্টিকে এককথার লোক বা Folk বলা যায়। আর এই 'লোক সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য মুখ্যত মৌখিক এবং ঐতিহ্যবাহী।
লোকসাহিত্য কি বা কাকে বলে :-
লোকসাহিত্য কি বা তার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গেলে আমাদের আগে জানা দরকার ‘লোক' বলতে আমরা কি বুঝি।
'লোক' বলতে এখন আর কেবলমাত্র গ্রামের ওই কৃষিজীবী ঐতিহ্যবাহী নিরক্ষর জনগণকেই বোঝায় না। আজ 'লোক'-এর সংজ্ঞার বিস্তার ঘটেছে, এখন 'লোক' বলতে আমরা বুঝি – সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কোন সূত্রে যদি বেশ কিছু মানুষ একত্রিত বা সঙ্ঘবদ্ধ হন, তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে সংহত নির্দিষ্ট ওই জনসাধারণকেই 'লোক' বলি।
'লোক' বলতে এখন আর কেবলমাত্র গ্রামের ওই কৃষিজীবী ঐতিহ্যবাহী নিরক্ষর জনগণকেই বোঝায় না। আজ 'লোক'-এর সংজ্ঞার বিস্তার ঘটেছে, এখন 'লোক' বলতে আমরা বুঝি – সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কোন সূত্রে যদি বেশ কিছু মানুষ একত্রিত বা সঙ্ঘবদ্ধ হন, তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে সংহত নির্দিষ্ট ওই জনসাধারণকেই 'লোক' বলি।
আরও পড়ুন :- লোকসংগীত কি?
এই সংজ্ঞায় 'লোক' বলতে যাদের বুঝি তারা আর কেবল গ্রামীণ কৃষিজীবী সম্প্রদায় নন, নন কেবল নিরক্ষর সংহত সমাজের সদস্য – এখানে গ্রাম-শহরের, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মৌখিক ও লিখিতের, কৃষি ও শিল্পের সকল ভেদাভেদ দূর হয়ে যায়। নিরক্ষরের পাশাপাশি, শিক্ষিত মানুষও হয়ে যান লোক বা Folk.
সেই লোকসমাজের ‘সৃষ্ট' সাহিত্য লোকসাহিত্য, সৃষ্ট কিন্তু লিখিত নয়, এই কারণে যে, লোকসাহিত্য মুখ্যত মৌখিক। লোকসাহিত্য মৌখিক কথা নির্ভর। তার কোন লিখিত রূপ যেমন (সংরক্ষণ ব্যতীত) দরকার হয় না, তেমনি তার কোন নির্দিষ্ট রচয়িতা বা স্রষ্টা নেই।
শিষ্ট সাহিত্য যেখানে ব্যক্তির সৃষ্টি, লোকসাহিত্য সেখানে সমষ্টির সৃষ্টি। লোকসমাজের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এর সামাজিক সংহতি। লোকসমাজ এমনই সংহত যে, এর যে কোন সৃষ্টিতে স্রষ্টা খুঁজে পাওয়া ভার লোকসংস্কৃতির যে কোন দিকেই একথা সত্য। তাই বলে -
লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির যে কোন রূপ কখনই লোকসমাজের সকল মানুষ একজায়গায় বসে আলাপ-আলোচনা করে সৃষ্ট নয়, তার এক একটা ধারার সৃষ্টির পিছনে কোন না কোন একক মানুষের ভূমিকা শুরুতে হয়তো ছিল, কিন্তু সংহত সমাজের সমবেত আওয়াজের ভীড়ে হারিয়ে গেছে সেই একক মানুষের একক চেষ্টার নজির।
তাই সব মিলিয়ে, লোকসাহিত্য কাকে বলে? এর উত্তরে বলা যায় - লোকসাহিত্য হল সংহত একদল মানুষের সমবেত সাহিত্য সৃষ্টি, যা মূলত মৌখিক ও ঐতিহ্যবাহী, যার সৃষ্টি লিখন নয়, মুখের ভাষাকেন্দ্রিক।
আরও পড়ুন :- কবিতা কাকে বলে?
লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :-
সংস্কৃতির মতো সাহিত্যেরও দুটি শ্রেণী—লোকসাহিত্য ও শিষ্টসাহিত্য। লোকসমাজ-সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা। লোকসাহিত্য মূলত বাক্কেন্দ্রিক, ঐতিহ্যবাহী এবং মৌখিক। লোকসাহিত্য - ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, কথা, নাট্য, মঞ্চ ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে গড়ে ওঠে। লোকসংস্কৃতির মতো লোকসাহিত্যেরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন—- লোকসাহিত্য মূলত বাককেন্দ্রিক।
- লোকসাহিত্যের শিষ্ট সাহিত্যের মতো লিখিত রূপ নেই, Folk Literature is simply literature transmitted orally.' লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক। অর্থাৎ স্মৃতি আশ্রিত ও শ্রুতি বাহিত।
- কেবল মৌখিক নয়, ঐতিহ্যবাহীও, অর্থাৎ লোকপরম্পরায় লোকসাহিত্য মুখে মুখে বাহিত হয়। মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার হওয়ার পর এই শ্রেণীর লোকসংস্কৃতি অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা লোকসাহিত্য বলি সেগুলোর বহু অংশ আজ লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।
- লিখনপদ্ধতির সূত্র ধরে লোকসাহিত্য শিষ্ট সাহিত্যের অন্তর্গত হয়েছে যেমন তেমনি আবার শিষ্ট সাহিত্যের অনেক বিষয়ও লোকপরম্পরায় বাহিত হয়ে লোকসাহিত্যে পরিণত হয়ে গেছে।
- লোকসাহিত্য মূলত বাক্কেন্দ্রিক কিন্তু কথাসবর্ষ নয়। তার সঙ্গে শিল্প মাধ্যমের আরো একাধিক অনুবঙ্গ থেকে গেছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেমন, লোকনাট্য, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি। লোকনাট্যের সংলাপগুলো লোকসাহিত্যের বা বাক্কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান হলেও এর অভিনয়গত দিকটির মধ্যে আছে অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদান বা অভিনয় কেন্দ্রিকতা। আছে নাট্যশিল্পের একাধিক উপাদান। আবার লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও বাককেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে যুক্ত আছে যন্ত্রানুষঙ্গ ও গীত হওয়ার দিকটি।
- লোকসাহিত্য মৌখিক বা অলিখিত ও ঐতিহ্যবাহী হলেও সংরক্ষণের সুবিধার্থে লোকসাহিত্যের একটা লিখিতরূপ বর্তমানে স্বীকৃত।
- লোকসাহিত্য তার ঐতিহ্যবাহী রূপের সমান্তরালে বিবর্তিত রূপকেও জায়গা করে দিচ্ছে। অর্থাৎ লোকসাহিত্য আর কেবল ঐতিহ্যকেন্দ্রিক থাকছে না। লোকসাহিত্য ঐতিহ্য স্বীকরণের পাশাপাশি বর্তমানকেও ধারণ করছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক মৌখিক সাহিত্যও লোকসাহিত্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করছে।
- লোকসাহিত্যের প্রাচীন ধারণায় তা কেবল গ্রাম্যসাহিত্য বলেই পরিচিত ছিল। গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের সাহিত্যই (যা মূলত মৌখিক) ছিল একসময় লোকসাহিত্য।
- কিন্তু এখন লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপট পাল্টানোর সমান্তরালে লোকসাহিত্যের পরিধি বিস্তারিত হয়েছে। লোকসাহিত্য আর কেবল গ্রাম্যসাহিত্য নয়, নয় কেবলমাত্র কৃষিজীবীদের সাহিত্য। তা গ্রামের গণ্ডি ছেড়ে নাগরিক জীবনেও প্রবেশ করেছে।
লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তা নিরক্ষর জনগণের সাহিত্য। এ পরিচয়ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ লোকসাহিত্য আর নিরক্ষরের সাহিত্য নয়, তা শিক্ষিত মানুষেরও সাহিত্য। তবে, লোকসাহিত্য তখনই শিক্ষিত মানুষের বা নাগরিক মানুষের লোকসাহিত্য হয়, যখন নাগরিক শিক্ষিত মানুষ 'লোক' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। যখন কোন একটা নির্দিষ্ট সূত্র ধরে শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সামাজিক বেশ কিছু মানুষ এক হন বা সংহত হন, সে গ্রামের নিরক্ষর কিংবা শহরের শিক্ষিত, কৃষিজীবী কিংবা কারখানার শ্রমিক তখন সে সংহত জনসমষ্টিকে এককথার লোক বা Folk বলা যায়। আর এই 'লোক সমাজের সৃষ্ট সাহিত্যই লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য মুখ্যত মৌখিক এবং ঐতিহ্যবাহী।
আরও পড়ুন :- গীতিকা কাকে বলে?
এসব গেল শিষ্ট সাহিত্যের উপকরণসমূহ। শিষ্টসাহিত্যের সমান্তরালে লোকসাহিত্যের যে অলিখিত ধারা প্রবহমান তা এক ছাঁচে ঢালা কোন উপকরণে সীমাবদ্ধ নয়। লোকমানস ও তাদের অবসর বিনোদনের নানান পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকসাহিত্যও নানা প্রকরণে বিভক্ত। তবে শিষ্ট সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তা লিখিত। বইয়ের পাতাতেই শিষ্ট সাহিত্যের একরকম মুক্তি সীমাবদ্ধতা।
অন্যদিকে কোনরূপ লিখিত আকার পায় না বলেই লোকসাহিত্য আবার একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কাজে-কর্মে, আনন্দে-বিষাদে, অবসর বিনোদনে লোকসাহিত্যের উপকরণ নিত্যক্রিয়াশীল। বাক্কেন্দ্রিক এই লোকসাহিত্যের একাধিক উপকরণ এগুলো হল - ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, কথা, নাট্য, মক্ত ইত্যাদি।
লোকসাহিত্যের উপকরণ :-
সাহিত্য হল সহিতের ভাব, যা সহিতত্ত্ব স্থাপন করে, তাই সাহিত্য, সাধারণ সাহিত্যের একটা লিখিত রূপ থাকে। এই লিখিতরূপের প্রকাশ কখনও গদ্যে, কখনও পদ্যে। গদ্য ও পদ্যকে শিষ্ট সাহিত্যের নানান উপকরণের আবির্ভাব—কাব্য, কথাসাহিত্য ও নাটক।- কাব্য আবার নানান রকম — আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, গীতিকাব্য ইত্যাদি।
- কথাসাহিত্য – উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি।
- নাটক—ট্র্যাজেডি, কমেডি, একাঙ্কনাটক ইত্যাদি।
এসব গেল শিষ্ট সাহিত্যের উপকরণসমূহ। শিষ্টসাহিত্যের সমান্তরালে লোকসাহিত্যের যে অলিখিত ধারা প্রবহমান তা এক ছাঁচে ঢালা কোন উপকরণে সীমাবদ্ধ নয়। লোকমানস ও তাদের অবসর বিনোদনের নানান পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী লোকসাহিত্যও নানা প্রকরণে বিভক্ত। তবে শিষ্ট সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তা লিখিত। বইয়ের পাতাতেই শিষ্ট সাহিত্যের একরকম মুক্তি সীমাবদ্ধতা।
অন্যদিকে কোনরূপ লিখিত আকার পায় না বলেই লোকসাহিত্য আবার একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কাজে-কর্মে, আনন্দে-বিষাদে, অবসর বিনোদনে লোকসাহিত্যের উপকরণ নিত্যক্রিয়াশীল। বাক্কেন্দ্রিক এই লোকসাহিত্যের একাধিক উপকরণ এগুলো হল - ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, গীতিকা, কথা, নাট্য, মক্ত ইত্যাদি।
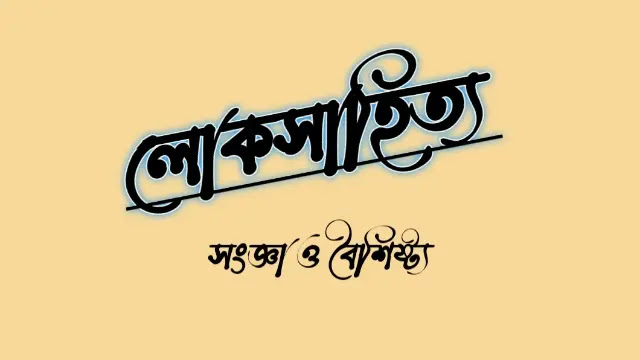
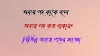






0 মন্তব্যসমূহ
Please do not enter any spam link in the comment box.